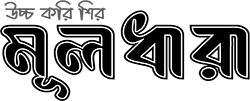সম্প্রতি ‘টাইমস হায়ার এডুকেশন’ ২০২৫ সালের বিশ্বসেরা ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। যথারীতি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এশিয়ার অনেক উন্নয়নশীল দেশও তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানে উন্নীত করে তালিকায় শক্ত অবস্থানের জানান দিতে সক্ষম হয়েছে। অথচ হতাশাজনক বাস্তবতা হলো, এই তালিকায় বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। এই সমস্যার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত গবেষণার প্রতি চরম অবহেলায়। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবকাঠামোগতভাবে পিছিয়ে রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষকের স্বল্পতাও শিক্ষার গুণগত মানকে বাধাগ্রস্ত করছে।
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা গবেষণা বাজেটের করুণ চিত্র একদিকে অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করে, অন্যদিকে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের দিকটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষায় গবেষণার জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৫০ কোটি টাকা। ভারতের আইআইএসসি (Indian Institute of Science) একাই বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা গবেষণা বরাদ্দ পায়। পাকিস্তানে প্রতি বছর গড়ে ১৫ হাজার গবেষণা প্রকাশিত হয়, যেখানে বাংলাদেশে এই সংখ্যা মাত্র ৪ হাজার ৫০০। মালয়েশিয়া জিডিপির ১.৪ শতাংশ গবেষণায় বিনিয়োগ করে, আর বাংলাদেশে তা ০.১ শতাংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে শুধুই পাঠদানের প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে এবং গবেষণার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বছরে গড়ে মাত্র ০.৩টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এটি কেবল শিক্ষকদের দায় নয়, গবেষণার জন্য পরিবেশ নেই, তহবিল সংকট, আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় শিক্ষকদের গবেষণার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফেরদৌসী ইসলাম বলছেন, ‘গবেষণার জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনিক জটিলতা শিক্ষকদের নিরুৎসাহিত করছে।
গবেষণাধর্মী শিক্ষাব্যবস্থা কেবল চাকরি পাওয়ার জন্য নয়; বরং নতুন জ্ঞান উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। অথচ আমাদের শিক্ষার্থীরা ভাবছেন, গবেষণা করলে সময় নষ্ট হবে, চাকরি মিলবে না। এই মানসিকতার পেছনে রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা—সর্বস্তরেই সৃজনশীলতার বদলে মুখস্থবিদ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে, গবেষণার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জন্মায় না, আর যারা আগ্রহী, তারাও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে পিছিয়ে পড়েন।
জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বা সিংগাপুরের দিকে তাকালে দেখা যায়, গবেষণাই তাদের মূল চালিকাশক্তি। অথচ বাংলাদেশে গবেষণাকে এখনো ‘অতিরিক্ত কাজ’ হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বের নামিদামি প্রতিষ্ঠান, যেমন আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, ইউনিসেফ, গুগল, নাসা—এসব জায়গায় ক্যারিয়ার তৈরির জন্য গবেষণা এখন প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার সুযোগ কম, ফলে তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।
এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এখনই কিছু কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। প্রথমত, গবেষণার বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো দরকার। শিক্ষা খাতের মোট বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ গবেষণায় বরাদ্দ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালাকে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের জন্য গবেষণার স্বাধীন পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালগুলোর সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে হবে এবং ডিজিটাল লাইব্রেরির সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প খাতের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করা গেলে গবেষণার বাস্তব প্রয়োগ বাড়বে।
লেখক : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী এবং ‘জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ফিচার, কলাম এন্ড কনটেন্ট রাইটার্স’-এর সদস্য