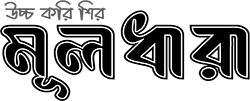সাধারণভাবে নৈতিকতা বলতে ব্যক্তির এমন এক মানসিক অবস্থাকে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন জড়িত থাকে, সেখানে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়—এমন পরিস্থিতির মধ্যে ভালো দিকটিকে গ্রহণ করার মানসিক ক্ষমতাই হলো নৈতিকতা। ভালো ও মন্দ বিষয় সম্পর্কে এক বা একাধিক সচেতন ও উত্কৃষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে নৈতিকতা বলা যায়। নৈতিকতা হলো এমন একধরনের মানদণ্ড বা আদর্শ, যার উত্পত্তি ঘটে ব্যক্তির বিবেক ও ন্যায়বোধ থেকে। যেক্ষেত্রে আইন ও ন্যায়নীতি অনুসরণ করা হয়, মন্দ দিক বর্জন করে ভালো দিকটি গ্রহণ করা হয় সেখানেই নৈতিকতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তাকেই বলা যায়, যিনি নিয়মনীতি ও আইনের পরিপন্থি কোনো কাজ করেন না বা এরূপ কাজ করতে কাউকে সহায়তাও করেন না। নৈতিকতার ঘাটতি থাকলে নানা দিক থেকে ব্যক্তি পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়; দেখা দেয় বহুমাত্রিক পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা। আর যারা রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে নৈতিকতার সামান্যতম ঘাটতি থাকলেও রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য তা সীমাহীন সমস্যা ও দুর্ভোগের সৃষ্টি করে। এ রকম ক্ষেত্রে উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করা উচিত। কারণ আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন উঁচু স্তরের অনেকেরই নৈতিকতা নিয়ে মাঝেমধ্যেই নানা ধরনের প্রশ্ন ওঠে। তাদের কেউ কেউ সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত লাভের বশবর্তী হয়ে নানা রকম অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে গণমাধ্যমে খবরও বের হয় প্রায়ই। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে দেখা যায়।
ব্যক্তিপর্যায়ে নৈতিকতার ঘাটতি থাকলে তা প্রাতিষ্ঠানিক বা রাষ্ট্রীয়পর্যায়ে কী পরিমাণ সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে, ব্যাংকিং খাত তার একটি অন্যতম উদাহরণ। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কিছু অংশের মধ্যে নীতি-নৈতিকতায় কতটুকু বিপর্যয় ঘটলে ব্যাংক থেকে বেআইনিভাবে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা বের হয়ে যায়, তা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও উচ্চপর্যায়ে কর্মরত থেকেও কীভাবে নিজের আয়ত্তাধীন বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ রাখা যায়, তা-ও আরেক বিস্ময়ের ব্যাপার। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এসব অর্থসম্পদ আইনসম্মতভাবেই অর্জিত হয়েছে; তবুও তার প্রকৃত ফয়সালা এখন আদালতের মাধ্যমেই হতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস, নিয়োগ-বাণিজ্য, টেন্ডার-বাণিজ্য, রেলের টিকিট-বাণিজ্য, বাজার-সিন্ডিকেট, শিক্ষার্থী ভর্তি-বাণিজ্য, অবৈধ অর্থে অর্জিত জমিতে রিসোর্ট গড়ে তোলা, সরকারি স্থাপনা দখল ইত্যাদির সবকিছুর পেছনেই অনৈতিক কার্যকলাপ ও অপশাসনের কুপ্রভাব লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্র থেকে এসব অনৈতিকতা ও অপশাসন নির্মূল করতে হলে দরকার উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরি করা। উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরি এবং রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে দরকার গুণ ও মানসম্মত শিক্ষা। কিন্তু লক্ষণীয়, আমাদের শিক্ষার মধ্যেই বড় ধরনের গলদ রয়েছে। শিক্ষা রাষ্ট্রের সবচেয়ে বৃহত্ একটি ক্ষেত্র, যার সঙ্গে দেশের কোটি কোটি মানুষ জড়িয়ে আছে। অথচ সেই শিক্ষাব্যবস্থাই আজ নানা ধরনের সমস্যার সংকটে আবর্তিত হচ্ছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু ভালো মানুষ তৈরি করতে পারছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই এখন ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এটা অধিক প্রত্যাশিত।
ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নৈতিকতার অনুশীলন ও কঠোর প্রয়োগ এবং রাষ্ট্রের সর্বত্র সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। রাষ্ট্রে সুশাসন থাকলে দেশ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যখন নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন বোঝা যায়, রাষ্ট্রের কোথাও না কোথাও নৈতিকতা এবং সুশাসনের অভাব রয়েছে। সুশাসন বা আইনের শাসন নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রথমত রাষ্ট্রের। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। নাগরিক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে—রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা, দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া, অন্যের আইনানুগ অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা, ন্যায়নীতিবহির্ভূত কার্যক্রম বর্জন করা, সর্বোপরি উচ্চ নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা ইত্যাদি। যে দেশের নাগরিকরা উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং যারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সে দেশ কখনো উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে না। নাগরিকরা যদি রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়মনীতি যথাযথভাবে মেনে চলে, তাহলে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি গঠনের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিক বিবেচনায় একটি ভালো রাষ্ট্র গঠনের জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ অর্থে সুশাসন হলো এমন এক প্রক্রিয়া, যা কোনো দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। সুশাসনের বহুমাত্রিক ধারণা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুশাসন ইত্যাদি। রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সুশাসন জরুরি। বিশ্বব্যাংকের মতে (১৯৮৯), সুশাসন হলো এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ সমাজের সমস্যা ও চাহিদা পূরণে ব্যবহূত হয়।
সুশাসন বলতে সাধারণভাবে বোঝা যায়, যে শাসনব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রের নাগরিকরা তাদের সম্ভাব্য আইনানুগ চাহিদা ও অধিকার বিনা বাধায় পরিপূরণ বা অর্জন করতে পারেন তা-ই হলো সুশাসন। কোনো দপ্তরে কোনো নাগরিকের কোনো আবেদনপত্র তুচ্ছ অজুহাতে অযৌক্তিকভাবে দিনের পর দিন আটকে রাখাকে সুশাসন বলে না। রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিককে আইনসম্মত অধিকারবঞ্চিত করে হয়রানি করা সুশাসন নয়। নাগরিকদের সহযোগিতা করা রাষ্ট্রীয় সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুশাসন মানে হলো—দায়িত্বশীল ও দক্ষ, স্বচ্ছ এবং অনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে আইনসম্মত উপায়ে পরিচালিত কার্যকর প্রশাসন। যথাসময়ে সরকারি কার্যসম্পাদনের সিদ্ধান্ত প্রদানও সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধ করে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা, রাষ্ট্রের সর্বত্র দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, আইনের শাসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। সুশাসনের মাধ্যমে জনগণের জন্য প্রদত্ত সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও সহজ করা হয়ে থাকে।
এখন চলছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা। আগামী জাতীয় নির্বাচনও এ আলোচনার কেন্দ্র্রবিন্দুতে রয়েছে। সংষ্কারের জন্য রাষ্ট্র যেমন উদগ্রীব হয়ে কাজ করে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোও সংস্কার নিয়ে নানা ধরনের মতামত প্রকাশ করে চলেছে। কিন্ত রাষ্ট্রে নৈতিকতার উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য তেমন কোনো আলোচনার খবর চোখে পড়ে না। অথচ সংস্কারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিকতার উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু সংস্কারের চেয়ে নৈতিকতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা আরো জরুরি। কারণ রাষ্ট্রে যতই সংস্কার করা হোক না কেন যদি নৈতিকতা ও সুশাসনের ঘাটতি থাকে, তাহলে সংস্কার কোনো কাজে আসবে বলে মনে হয় না। অন্য কথায়, নৈতিকতা ও সুশাসনের ঘাটতি থাকলে দেশে নানামুখী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করবে, রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটবে। আমরা মনে করি, সংস্কার ছাড়াও নৈতিকতার উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব।
লেখক : অধ্যাপক (শিক্ষা) ও সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা), ময়মনসিংহ
(এই লেখা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত। এ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়ভার লেখকের ওপর বর্তাবে এবং এর জন্য দৈনিক মূলধারা কোনোক্রমেই দায়ী নয়। )