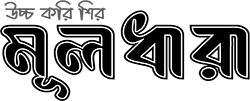বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে প্রকৃতির ভয়াবহ রূপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে মানবজাতিকে। বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে সতর্ক করে আসছেন, জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন ও উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবী যে বিপদে পড়তে পারে, তা কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসব সতর্কবাণীকে আরো দৃঢ় করেছে। লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল, ভারত মহাসাগরে ঘনঘন সাইক্লোন এবং বরফ গলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যা আমাদের এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
লস অ্যাঞ্জেলস এবং এর আশপাশের এলাকা বিশ্বের অন্যতম দাবানলপ্রবণ অঞ্চল। লস অ্যাঞ্জেলসের মালিবু এলাকা বারবার দাবানলের কবলে পড়েছে। এটি উত্তর আমেরিকার অন্যতম বেশি দাবানলপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। ১৯৯৮ সালে পরিবেশবিদ মাইক ডেভিস উল্লেখ করেছিলেন যে, মালিবুতে প্রতি দুই থেকে আড়াই বছর পরপর বড় ধরনের দাবানল ঘটে। গরম, খরা এবং শক্তিশালী বাতাসের কারণে এখানে প্রায়ই ভয়াবহ দাবানল সৃষ্টি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এই পরিস্থিতিকে আরো ভয়ংকর করে তুলছে। কারণ এটি পৃথিবীর আবহাওয়াকে আরো উষ্ণ ও শুষ্ক করে তুলেছে। ফলে আগুনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা ক্রমাগত বাড়ছে।
২০২৪ সালের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস ও আশপাশের বনাঞ্চলে দাবানল ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে দাবানল এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। গবেষকরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এবং বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা বাড়ায় দাবানলের ঝুঁকি দিনদিন বাড়ছে। দাবানল এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রায় ৫০ হাজার একর জমি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয়রা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।
অঞ্চলটি আগে থেকেই শুষ্ক এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মাটি ও গাছপালা আরো শুকিয়ে গেছে, যা দাবানল ছড়ানোর পরিবেশ তৈরি করেছে। এছাড়া, বাতাসের গতিবেগ দাবানলকে আরো বিধ্বংসী করে তোলে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই দাবানলের কারণ হিসেবে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্রমবর্ধমান মাত্রা, গ্রীষ্মের দীর্ঘায়িত সময় এবং বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তাকে দায়ী করা যায়।
লস অ্যাঞ্জেলসের এই পরিস্থিতি থেকে স্পষ্ট যে, এমন দুর্যোগ ভবিষ্যতে আরো ঘন ঘন ঘটতে পারে, যদি আমরা কার্যকর পদক্ষেপ না নিই। বিভিন্ন সময়ের উল্লেখযোগ্য দাবানল পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখি যে, ২০২৪ সালের ফ্র্যাঙ্কলিন ফায়ারে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় মালিবুর ৪ হাজার একর এলাকা পুড়ে যায়। ২০১৮ সালের উলসি ফায়ারে প্রায় ৯৬ হাজার ৯৪৯ একর পুড়ে যায় এবং ধ্বংস হয় ১ হাজার ৬৪৩টি বাড়িঘর। ২০০৯ সালের স্টেশন ফায়ার পুড়িয়ে দেয় ১ লাখ ৬০ হাজার ৫৭৭ একর এলাকা। ১৯৭০ সালের মালিবু ফায়ার ছয় মাসের খরার পর ৩১ হাজার একর এলাকা ধ্বংস করে এবং ১০ জনের প্রাণহানি ঘটায়।
লস অ্যাঞ্জেলসে দাবানলের পেছনে প্রধান কারণ সান্তা আনা বাতাস। শরতের মরুভূমি থেকে আসা এই শক্তিশালী বাতাস দাবানলকে আরো তীব্র করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালে সান্তা আনা বাতাস ওকল্যান্ডে আগুন ছড়িয়ে মাত্র দুই দিনে ৩ হাজার বাড়ি ধ্বংস করে দেয়।
খরা ও দাবদাহ যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের খরার হার বেড়ে গেছে। দীর্ঘ সময় ধরে শুষ্ক আবহাওয়া এবং শুকনো গাছপালা দাবানলের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ যা পাহাড়ি এলাকা, বনভূমি ও গুল্মভূমির আশপাশে বাড়ি তৈরি করা এবং দমন ব্যবস্থার অভাবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
দাবানল শুধু জীবন এবং সম্পদ নয়, পরিবেশের জন্যও বড় ধরনের হুমকি। বনভূমি ধ্বংস হওয়ায় প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান নষ্ট হয় এবং কার্বন নিঃসারণ বাড়ে। মূলত, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই উষ্ণতা ও শুষ্কতার মাত্রা বাড়ছে। যা দাবানলকে তীব্রতর করে তুলছে। যার প্রধান কারণই হলো দীর্ঘস্থায়ী খরা, উষ্ণ বাতাসের প্রভাব, বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তন।
শুধু কি দাবালনের ভয়াবহতাই বাড়ছে, মহাসাগরগুলোতে ভয়ংকর সাইক্লোনের দাপট দেখা গেছে। গেল ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভারত মহাসাগরসহ চারটি মহাসাগরে পরপর বিধ্বংসী চেহারার সাইক্লোন সৃষ্টি হয়। যেগুলোর মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ে কয়েক হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হয়। বাস্তুচ্যুত হয় প্রায় ১০ লক্ষাধিক মানুষ। এমন ঘন ঘন সাইক্লোনের সৃষ্টি জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব হিসেবে ধরা হয়। বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে সাইক্লোনের শক্তি ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত মহাসাগরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার ফলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা সাইক্লোনের শক্তি বাড়ায়। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি বহুগুণ বেড়ে গেছে।
বরফ গলে সৃষ্ট বন্যার ভয়াবহতা দেখতে পাই ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় অঞ্চলে বরফ গলে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। নেপাল, ভারত এবং পাকিস্তানের বহু অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যায়। হিমালয়ের হিমবাহ থেকে গলে আসা পানি নদীর প্রবাহকে এত বেশি বাড়িয়ে দেয় যে, তা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমবাহগুলো দ্রুত গলছে। শুধু হিমালয় নয়, গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকার বরফের স্তরও একই পরিণতির মুখে। বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে বন্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করছে।
বিশ্ব জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বহুমাত্রিক। এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশকে নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিকেই হুমকির মুখে ফেলছে। বিশেষ করে কৃষিতে অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কারণে ফসল উত্পাদন হ্রাস পাচ্ছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক অঞ্চলে খাদ্যসংকট বাড়ছে। জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি চোখে পড়ে, যেমন মেরু অঞ্চলের প্রাণী থেকে শুরু করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ, সবই বিপন্ন হয়ে পড়ছে।
বিশ্ব উষ্ণায়নের সবচেয়ে বেশি শিকার হওয়া দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। এর কারণ ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং দুর্বল অবকাঠামো। আমাদের দেশে উপকূলীয় অঞ্চলে ঝুঁকি কম নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপগুলো ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশের খরা ও বন্যার অনন্য উদাহরণ দেখা যায় বরেন্দ্র অঞ্চলে। এখানে খরার প্রকোপ বেড়েছে, আবার পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীতে বারবার বন্যা দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান, বুলবুলের মতো দুর্যোগের তাণ্ডব দিন দিন বাড়ছে।
আমাদের দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণগুলোর মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসারণ অনেকটাই দায়ী। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন উজাড় ও আরেকটি কারণ। বনভূমি ধ্বংসের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। অন্য আরেকটি কারণের মধ্যে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ।
জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হলে বাংলাদেশকে আরো সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এজন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ঘটাতে হবে। আর এজন্য সৌরশক্তি, বায়ুশক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বন সংরক্ষণের বিষয়টি জোরালোভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে আর এজন্য উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাড়ানো ও দেশের অভ্যন্তরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। খরা ও বন্যা মোকাবিলা করার জন্য জলাধার নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও পানি সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে হবে। জলবায়ু তহবিল আরেকটি উপায় হতে পারে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, তা দেশের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। সর্বোপরি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে আর এজন্য জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আর তার প্রধান উপায় কার্বন নিঃসারণ কমানো। উন্নত দেশগুলোকে তাদের কার্বন নিঃসারণ সীমিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয়ত প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন করতে হবে। প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পদক্ষেপ নিতে হবে। তৃতীয়ত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রয়োজন। বর্জ্য থেকে শক্তি উত্পাদন এবং কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্বউষ্ণায়ন এখন আর ভবিষ্যতের সমস্যা নয়; এটি আমাদের বর্তমান বাস্তবতা। লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল, ভারত মহাসাগরের ঘন ঘন সাইক্লোন ও বরফ গলে সৃষ্ট বন্যাপ্রকৃতির এমন বার্তা অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য এই পরিবর্তন আরো চ্যালেঞ্জিং। তবে সঠিক পরিকল্পনা, জনগণের সচেতনতা ও বৈশ্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব। এখন সময় এসেছে প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার। বর্তমানের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করতে পারে।
লেখক : শিক্ষক, গবেষক জলবায়ু-পানি