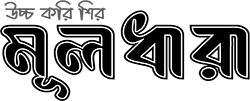দেশে নতুন করে ভ্যাট আরোপ নিয়ে বিতর্ক চলছে। গত ১১ জানুয়ারি বিবিসি নিউজ বাংলার অনলাইনের এক সংবাদ বিশ্লেষণের শিরোনাম ছিল : ‘শতাধিক পণ্য ও সেবায় সরকার ভ্যাট বাড়ানোর পথ বেছে নিল কেন। এতে শুরুতেই বলা হয়েছে : ‘‘বাংলাদেশে অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে হুট করে শতাধিক পণ্য ও সেবায় মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট বাড়ানোর পাশাপাশি ট্রাকে করে টিসিবির পণ্য বিক্রি বন্ধ হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক দল ছাড়াও অর্থনীতিবিদ ও ভোক্তারা সরকারের এ পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন।…অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রাজস্ব আদায়ে ধস নামার প্রভাব ঠেকাতে এবং আইএমএফের কাছ থেকে অতিরিক্ত ১ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার জন্যই সরকার ‘কর আদায়ের এ সহজ পথ’ বেছে নিয়েছে।’’
অবশ্য ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘বিগত পাঁচ মাসে ৪২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ৬৯ হাজার কোটি টাকা, সেখানে সংগ্রহ হয়েছে ১ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকার একটু বেশি। এছাড়া বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে ট্যাক্স আদায়ের হারও অনেক নিচের দিকে। অনুপাতের হার এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে যে, সেটি টেকসই নয়। বাংলাদেশের মানুষের ভালো থাকার জন্য ট্যাক্স জিডিপির রেশিও একটা জায়গায় নিতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে।’ তিনি ভ্যাটের সরলীকরণ করা হলে লিকেজ কমে যাওয়ার কথা বলেছেন। একই সঙ্গে এতে সাধারণ মানুষের ওপর তেমন কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য করেছেন। গত ২ জানুয়ারি অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন কথাই বলেছিলেন।
২০২৩ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণের অনুমোদন দেয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। এই ঋণের তিন কিস্তির টাকা ইতিমধ্যেই ছাড় করা হয়েছে এবং চতুর্থ কিস্তির টাকাও দেওয়া হবে বলে জানা যায়। তবে এরই মধ্যে আইএমএফের কাছ থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে আরো ১ বিলিয়ন ডলার সহায়তা চাওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, আইএমএফের সঙ্গে আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দরকষাকষিতে অদক্ষতার কারণেই এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতির এ সময়ে ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে সরকারকে।
এর আগে ভ্যাট বাড়ানোর সুবিধার্থে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ২০২৫-এর খসড়া সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে গত ১ জানুয়ারি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। যেসব পণ্যে ভ্যাট ও শুল্ক বেড়েছে তা হলো : এলপি গ্যাস, বিস্কুট, আচার, টম্যাটো কেচাপ, সস, ফলমূল, সাবান, মিষ্টি, ডিটারজেন্ট, চপ্পল (স্যান্ডেল), টিস্যু পেপার, ইন্টারনেট, বিমান টিকিট, সিগারেট, বিস্কুট, হোটেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতির পণ্য ও সেবায়।
উল্লেখ্য, ঋণ দিতে আইএমএফ বাংলাদেশকে কর-জিডিপি অনুপাত ০.২ শতাংশ বাড়ানোর শর্ত দিয়েছে, টাকার অঙ্কে যা ১২ হাজার কোটির বেশি। এই অর্থ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার সঙ্গে যোগ হবে। জুলাই-আগস্টের আন্দোলন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নানাবিধ সংকটে রাজস্ব আদায়ের পরিস্থিতি ভালো নয়। চলতি অর্থবছরের চার মাসেই রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। এমন অবস্থায় বাড়তি রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্যই যে ভ্যাট বাড়ানোর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
এর আগে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে দাবি করেন, ‘কর বাড়লেও জিনিসপত্রের দামে প্রভাব পড়বে না। আমাদের মূল্যস্ফীতির মূল ওয়েটের ইন্ডিকেটরগুলো হলো চাল, ডাল এগুলো। আমরা যেসব জিনিসের ওপর কর বাড়াচ্ছি, এগুলো মূল্যস্ফীতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ’। তার সাফ কথা হলো :‘পৃথিবীর কোনো দেশেই, এমনকি নেপাল, ভুটানেও বাংলাদেশের মতো এত কম কর (ট্যাক্স) নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় বলেছি, সেখানে আমরা প্রায় জিরো করে নিয়ে আসব।’
তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, নতুন ভ্যাটের ফলে মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে। এতে সাধারণ মানুষ আরো চাপে পড়বে। কেননা এই ভ্যাট তো ব্যবসায়ীরা দেবেন না। এটার চাপ পড়বে ভোক্তাদের ওপর। অথচ তাদের আয় বাড়ছে না। কিন্তু খরচ আরো বাড়ছে। ফলে তারা ব্যবহার কমিয়ে দিতে বাধ্য হবে অথবা ঋণগ্রস্ত হবে।
সরকারের এই সিদ্ধান্তে রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে ওষুধশিল্প, মোবাইল ফোন অপারেটর, হোটেল ও রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ীরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাদের কথা, এই ভ্যাটের ফলে তাদের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গ্রাহক হারাবেন, বিক্রয় কমবে। ভ্যাটের বাইরেও তাদের আরো ট্যাক্স দিতে হয়। ফলে এখন পণ্যের দাম আরো বেড়ে যাবে। এমনিতেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। আরো দাম বাড়লে তারা কেনা কমিয়ে দেবেন। ফলে ব্যবসায়ী ও ভোক্তা উভয় পক্ষই ক্ষতির মুখে পড়বে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, সরকার যে এত বড় সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলল না, এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানল না। মনে হলো, ভ্যাট বাড়িয়ে দিল। এটা তো হয় না। এখন সাধারণ মানের হোটেলেও এক জনকে খেতে ৩০০ টাকা লাগবে—সেটা কতজন খেতে পারবে। এমনিতেই ব্যবসা নেই। আরো ধস নামবে।
এদিকে দেশে মূল্যস্ফীতির খবর সুখকর নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, গত নভেম্বর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১৩.৮০ শতাংশে ঠেকেছে। এটি গত ১৩ বছরের মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার। গত জুলাই মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪.১০ শতাংশে উঠেছিল। নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়ার পাশাপাশি সার্বিক মূল্যস্ফীতিও বেড়ে ১১.৩৮ শতাংশে উঠেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ১০০ টাকায় যে পণ্য ও সেবা কেনা গেছে, গত বছরের নভেম্বরে একই পরিমাণ পণ্য ও সেবা কিনতে ভোক্তাকে ১১১ টাকা ৩৮ পয়সা খরচ করতে হয়েছে। ডিসেম্বরের মূল্যস্ফীতির হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি।
সরকারের রাজস্ব দরকার, রাজস্ব না বাড়লে দেশের উন্নয়ন হবে কীভাবে? কিন্তু এই মুহূর্তে ভ্যাট না বাড়িয়ে এনবিআরের এনফোর্সমেন্টে যে সমস্যা আছে, সেটা দূর করতে অধিক মনোনিবেশ করা যেত। ট্যাক্স আদায়ে দুর্বলতা কমালে রাজস্ব আদায় বাড়ত। আবার অনেকেই ট্যাক্স নেটের আওতায় নেই, অথচ তারা ট্যাক্স দেওয়ার যোগ্য। তাদের করের আওতায় আনতে পারলেও ট্যাক্স আদায় বাড়ত।
আসলে এখন এভাবে ভ্যাট আরোপ করলে মানুষের কষ্ট বাড়বে। আবার ইনকাম ট্যাক্সও এখন বাড়ানো যাবে বলে মনে হয় না। উপায় হলো বিনিয়োগ বাড়ানো। তার জন্য ব্যাংক সুদের হার কমাতে হবে আর এনবিআরে দুর্নীতি কমাতে হবে। এটার উপায় হলো, ট্যাক্স সিস্টেমকে অটোমেশন করা। সেটা করা হলে ট্যাক্স আদায় বেড়ে যাবে। ট্যাক্স নেটও বাড়ানো যাবে। যে ২০-৩০ শতাংশ কর ফাঁকির ঘটনা ঘটে, সেটা বন্ধে এনবিআরকে উদ্যোগ নিতে হবে। করপোরেট ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স নেট বাড়ানো হচ্ছে না। এনবিআরের একশ্রেণির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে সহায়তা করে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ৫ আগস্টের পরেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে ভ্যাট বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের গলাকাটার পথ কি তৈরি করা হচ্ছে না? অভিযোগ রয়েছে, এনবিআরের অনেক কর্মকর্তা করপোরেটদের এজেন্ট। তাদের কাজ হলো, করপোরেটরা কীভাবে কর ফাঁকি দিতে পারে, তার বন্দোবস্তু করা। এক্ষেত্রে কার্যকর সংস্কার না করা গেলে রাজস্ব আদায় বাড়বে না।
লেখক : সাবেক কর কমিশনার ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল এফএফ ফাউন্ডেশন
(এই লেখার সম্পূর্ণ দায়ভার লেখকের একান্ত নিজের। এ সংক্রান্ত বিষয়ে দৈনিক মূলধারা কোনোভাবেই দায়ী নয়)