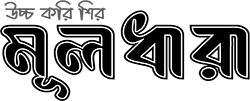সুখ কী? প্রকৃতপক্ষে সুখের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। সুথ একটি আপেক্ষিক বিষয়। কেউ অল্পতেই সুখী। কেউ অনেক কিছু পেয়েও সুখী নয়। আরো বেশি চাই। সমাজতত্ত্ববিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা সুখের সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন ধর্মবেত্তারা। তারা অবশ্য অল্পতেই সুখের ঠিকানা খুঁজে নিতে উপদেশ দিয়েছেন মানুষকে। আবার কবি হা-হুতাশ করে বলেছেন, ‘হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে যাও সুখের সন্ধানে’। সুখ নিহিত রয়েছে মানুষের মধ্যেই—শরীরে ও মনে। কথায় বলে, ‘সুস্থ দেহে, সুস্থ মনের যোগফল সুখ’। আবার বিপরীতে ‘মন ভালো তো শরীর ভালো’। উপলব্ধি হয় সুখানুভূতি।
আন্তর্জাতিক সুখী দিবসের ধারণা প্রথম দেন বিশ্বের অন্যতম ভিলানন্ত্রপিস্ট বা মানবহিতৈষী জাতিসংঘের বিশেষ উপদেষ্টা জায়মি ইলিয়েন, মহামতি মাদার তেরেসার হাত ধরে যার বিশ্ব। আমাদের জীবন ইচ্ছার কাছে বন্দি। আর যে জীবন ইচ্ছার যতটা অধীন, সেই জীবন ততটাই দুঃখময়। যুক্তি বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাই জীবনের চালিকাশক্তি। ইচ্ছা হলো সেই অন্ধশক্তি, যা সবকিছুর মূল চালক মানুষের মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকার ইচ্ছা, অগ্রগতির ইচ্ছা এবং সর্বোপরি সম্মী হওয়ার ইচ্ছা। এই ইজ্য একটি সহজাত প্রবৃত্তির মতো, অনেকটা আবশ্যিকভাবে আমাদের টেনে নিয়ে চলে জীবনের জটিলতার দিকে, সুখ চাওয়ার দিকে।
মানুষের চেতনা আছে, আভাগচেতনতা ও বৃদ্ধি আছে, তাই জীবনের অনেক লোভ-লালসা-আনন্দ আমাদের হাতছানি দেয়। আমরা জীবনের মোহে পড়ি। আমরা ছুটে চলি অবস্থার উন্নতির জন্য। ভালো বেতনের কাজ খুঁজি, ভালো সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজি। আমরা পদ-পদবির লোড করি, ক্ষমতা যানের চেষ্টা করি। মানুষের ওপর প্রতার খাটাতে চাই, এসবই আমরা করে থাকি আয়াসুখের অদম্য ইচ্ছার দ্বারা চালিত হওয়ার আরণে অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন, সুখ হলো জেনেটিক বা বংশানুগতিসম্বন্ধীয়। আবার কিছু বিজ্ঞানী তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্র ধরে বলেছেন, তারা মতিমের এমন কিছু অংশ নির্ণয় করেছেন যেখান থেকে সুখ নিঃসৃত হয়। জেনেটিক বা বংশানুগতিসম্বন্ধীয় সুখ অনেকাংশেই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অনুভূতি। এটি অনেকটা মানুষের কোলেস্টেরল লেভেলের মতো, যা জেনেটিক্যালি প্রভাবান্বিত, আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ মানুষের আচার-অক্ষরণ বা লাইফস্টাইল এবং খাদ্যাঙ্গাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
সুখকে মাঝে মাঝে একধরনের স্বার্ধিক উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়। মানুষের কী আছে তার ওপর মুখ নির্ভর করে না। মানুষ কী ভাবে বা কীভাবে চিন্তা করে-আার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সুথ। যার যা আছে কিংবা যে অবস্থায় আছে, তার জন্য শোকরিয়া জানিয়ে যদি দিন শুরু করা হয়- তাতে মুখ আসবে। কাজকর্ম ও চিন্তাধারায় পড়িটির অ্যাগ্রেড নিয়ে শুরু করলে জীবনে সুফল আসবে আত্মবিশ্বাদে বিশ্বাসী, মর্যাদাবান, হৃদ্যয়্যবান, জ্ঞানী-গুণী, সৎ মানুষ সাধারণত সব সময় সুখী হয়। যারা শুধু নিতে চায়, নিতে জানে না বা চায় না, তারা সুখী হয় না।
প্রত্যেক অভিজ্ঞ মানুষই বলে থাকেন যে, সুখপ্রাপ্তির জন্য শর্টকাট কোনো রাস্তা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষরাও দিনের ২৪ ঘণ্টা সুখী হয় না কিংবা থাকে না। সুখী মানুষের জীবনেও হতাশা, স্থঃখ-কষ্ট আসে। পার্থক্য হলো সুখী মানুষরা হতাশা, সুখে-কষ্টকে সহজভাবে গ্রহণকরতে পারে। অনল্লা যা পারেনা আমাদের শরীর শুধু রক্ত-মাংসে গড়া কোনো জড়বত্র নয়। আমাদের আত্মা আছে, যা শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবেগ-অনুভূতি আমাদের শরীরের ওপর প্রচন্ড প্রভাব ফেলে থাকে। বস্তুজগতে কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, মোহ, মাৎসর্য, ঈথা ও প্রতিহিংসা আমাদের স্নাখ, কষ্ট, অশান্তি, অসুখী ও ধ্বংসের কারণ। মানুষ তার সততা, সৎকর্ম ও অটল সৃষ্টিকর্তাপ্রতি দিয়ে উল্লিখিত বদগুণ থেকে নিজেকে দূরে রেখে এই পার্থিব জীবনেই পরম স্বর্গসুখের স্বাদ লাও করতে পারে। অন্যের সঙ্গে আাপাচাপি করতে পারাই প্রকৃত সুখ।’ মনের আনন্দ, সুখ অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি না করতে পারলে সেটা কোনো আনন্দই নয়। সুখ অনেকাংশেই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অনুভূতি। এটি অনেকটা মানুষের কোলেস্টেরল লেভেলের মতো, যা জেনেটিক্যালি প্রভাবিত ছলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের আচার-আচরণ বা লাইফস্টাইল এবং খাদ্যাভ্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
সবাই সুখী হতে চায়। সুখের সংজ্ঞা ব্যক্তি বিশেষে চিন্ন। । বিপুল অর্থ-সম্পদের মধ্যেই কি জীবনের সব সুখ মেলে? মুখ অনুভূতির পুরোটাই কি অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব। সন্তষ্টি লাভের পথে অথই কি শেষ কথা? নাকি জীবনে অন্যকিছুরও প্রয়োজন রয়েছে? অর্থ অর্থ সুখ কিনতে পারে না। হয়তো অণিকের সুখ দিতে পারে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, সুখের জন্য অর্থ খুব জরুরি নয়।
গবেষকরা মনে করেন, অর্থ ব্যয় করে মানুষ যে অসংখ্য জিনিস কেনে, তা তাদের সুথ অনুভূতির ওপর একটা বড় প্রভাব ফেলে। তারা মনে করেন, অর্থ দিয়ে কিছু কেনায় যে শান্তি আসে, তা মানসিক চাহিদা পুরণ করে; অর্থায় কোনো ব্যক্তি যদি অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু কেনার মাধ্যমে সুখ অনুভব করেন, তবে তা-ই তার সুখ। আবার ব্যক্তি বিশেষে বদলে যেতে পারে সুখের। সুথের সংজ্ঞা। পার্থিব জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা। অনস্বীকার্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। তবে জীবন চালাতে কতটা অর্থের দরকার, সেটি তর্কসাপেক্ষ। অনেকে আছেন, যারা অর্থ ছাড়া জীবনকে অথয়ন মনে করেন। যারা অত্ততে তুষ্ট নন তাদের জীবনদর্শন হলো দুনিয়াটা টাকার বশ তাই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা চাই। আবার অনেকে মনে করেন, মানবজীবনে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে এটা যেমন ঠিক, তেমনি বেশি অর্থ হয়ে ওঠে সব অশান্তির উৎস।
আসলে সুখ একটি মানবিক মানসিক অনুভূতি, অর্থাৎ সুখ মনের একটি অবস্থা বা অনুকৃতি, যা ভালোবাসা, তৃপ্তি, আনন্দ বা উচ্ছ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থ সব সময় সুখ দিতে পারে না সত্যি, কিন্তু একজন লোক যখন অন্যদের চেয়ে বেশি উপার্জন করেন, তখন তিনি নিজেকে। ঠিকই সুখী মনে করেন। একটি প্রবাদ রয়েছে, ‘অভাব যখন দরজায় এসে দাঁড়ায়, তখন সব ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়। তাই সুখের জন্য কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, তা নির্ধারণেরও প্রয়োজন রয়েছে। বলা হয়, মোটামুটি ভালোভাবে চলার জন্য যা খরচ হয়, সেই ব্যয় মেটতে পারলেই খুশি হয় মানুষ। অর্থের সঙ্গে সুখের সম্পর্ক যেমন জটিল, সঠিকভাবে সুখ পরমাপ করাও তেমনি কঠিন।
ধনী, গরিব, উঁচু-নিচু বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ রয়েছে। কিন্তু সুখী মানুষ খুঁজে পাওয়া সোনার পাথর বাটির মতো। সবাই সুখী হতে পারে না। সুদী সুম্বী হতে হলে অঢেল সম্পদ আর প্রাচুর্য থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। নিজের যতটক আছে তার মধ্যে সন্তুষ্ট থেকে আনন্দ খুঁজে পেলে সুখী হওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু মানুষের চাহিদার শেষ নেই। সে যত পয় অতই আমরা যখনই ‘অধিক’ (মোর) পেছনে ছুটল, তখনই শারীরিক ও মানসিক চাপের কারণে আমাদের সুখ ও শান্তি ভুলুণ্ঠিত হবে, আর আমরা যখন যথেষ্ট (এনাফ) বলতে শিখল তখন চাপমুক্ত থেকে সুখ ও শান্তি অনুভব করতে পারব।
একজন মানুষের কত টাকা লাগে? কিংবা একটা পরিবারেরই-বা কত টাকা লাগে? কত জমিজমা দরকার? খাই খাই স্বয়াবেরও তো একটা সীমারেখা থাকা দরকার। ক্ষমতা আছে বলেই কি যা খুশি তা-ই করব?
প্রত্যেকের জীবন শেষ হয়, কিন্তু চাহিদার শেষ হয় না। আমরা প্রত্যেকেই যেন ছুটে চলেছি অনন্ত এক চাহিদাকে সঙ্গী করে। মহাকালের আয়ুতে জীবনের দৌরাত্ম্য বড্ড ছোট রেখায়। একজন মানুষ, একটা পরিবারের সদস্যরা কী পরিমাণ বেতে পারেন? যে সম্পদে অনে অন্যের দীর্ঘশ্বাস লেগে থেকে, যে ক্ষমতায় অন্যকে প্রবঞ্চনার কাহিনি লেপটে থাকে, তা মানুষকে ভোগবাদী বানাতে পারে কিন্তু সুখী বানায় না। সুখ ভিন্ন বৃক্ষের ফল।
লেখক : ফিকামলি তত্ত্বের জনক, শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞান গবেষজ্ঞ