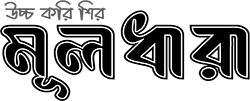বর্তমান বিশ্বের এমন একটি দেশও দেখানো যাবে না, যারা আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। কোনো দেশ যদি প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণও হয় কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে, তাহলে সেই দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং নতুন সম্পদ সৃষ্টিতেও জ্ঞানবিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝায় না। উন্নয়ন একটি সামগ্রিক ধারণা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অগ্রগতি অর্জন করাকেই উন্নয়ন বলা যেতে পারে। শিক্ষার প্রথম কাজই হচ্ছে দক্ষ ও উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা।
বাংলাদেশের মতো অধিক জনসংখ্যা-সংবলিত একটি দেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকরির মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তি খাতে কর্মসংস্থানের প্রতি আমাদের জোর দিতে হবে। আর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প নেই। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও সুবিধাজনক নয়। আত্মকর্মসংস্থান না করতে পারা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার বড় কারণ হচ্ছে, আমাদের শিক্ষার গুণমানের ক্রমঅধঃপতন। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বের হচ্ছেন। কিন্তু তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন না। কারণ তারা যে শিক্ষা অর্জন করেছেন, তা কর্মমুখী তো নয়ই, এমনকি মানসম্পন্নও নয়। অনেকেই বলে থাকেন, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বেকার সৃষ্টির কারখানা। একটি জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে—বাংলাদেশের শ্রমশক্তির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত বেকারের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রতি তিন জন উচ্চশিক্ষিত তরুণের মধ্যে এক জন বেকার। অনেকে হয়তো কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন কিন্তু সেজন্য তাকে অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। একজন শিক্ষার্থী যদি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন, তাহলে তাকে দীর্ঘদিন বেকার থাকতে হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি, যেখান থেকে উপযুক্ত আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষার্থী বেরিয়ে আসবেন।

শিক্ষার্থী-জনতার আন্দোলনের মুখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা। এর আগে তারা প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। বিভিন্ন খাতে বিদ্যমান পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা এবং তেপ্রক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছয়টি বিশেষ কমিশন গঠন করেছে। গঠিত কমিশনগুলো ইতিমধ্যেই তাদের প্রতিবেদন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধানের কাছে পেশ করেছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেই শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা অনুধাবন এবং বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। তাহলে কি শিক্ষা খাতে কোনো সমস্যা নেই? কোটা সুবিধা সংস্কারের দাবি পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি শিক্ষাব্যবস্থার সব সমস্যা দূরীভূত হয়ে গেল? বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা যেত, তাহলে অন্য অনেক সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যেত।
প্রয়োজনীয় অর্থায়নের অভাব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের পথে একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। অর্থাভাবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ইউনেসকোর মতে, একটি দেশের মোট জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত এই অর্থের বেশির ভাগই গবেষণাকার্যে ব্যবহূত হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে প্রতি বছর যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তার পরিমাণ জিডিপির ২ শতাংশেরও কম। এই বরাদ্দের অনুপাত প্রতি বছরই হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের একটি বড় অংশই অবকাঠামোগত নির্মাণকাজে ব্যয়িত হয়। তাই গবেষণাকাজে অর্থ পাওয়া যায় না। ফলে শিক্ষার মানের ক্রমবনতি ঘটছে। স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষার মানে অবনতি শুরু হয় এবং এখন তা প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।
শিক্ষার মানের যে কতটা অবনতি হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ষাটের দশকে আমাদের এই অঞ্চলে শিক্ষার যে মান ছিল, স্বাধীনতার পর তা ধীরে ধীরে অবনতি হতে থাকে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা যেসব গ্র্যাজুয়েটস তৈরি করছি, তারা কার্যত অর্ধশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটস। এদের অধিকাংশকেই সুশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটস বলা যাবে না। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞানচর্চা বলতে আমরা যেটা বুঝি, তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যে কারণে শিক্ষার এই নিম্নমান পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এর দুইটি কারণ চিহ্নিত করতে পেরেছি—প্রথমত, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, বাংলায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হবে। কিন্তু বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করতে হলে যে মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত বই-পুস্তকের জোগান নিশ্চিত করতে হবে, সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়নি। আর সেসময় সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার নামে আমরা আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করি, যার ফলে আমরা বাংলা ভাষাটাও সঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পারিনি। ইংরেজি ভাষাও শিখতে পারিনি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয় ইংরেজিতে। কাজেই ইংরেজি ভালোভাবে জানা না থাকলে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সঠিকভাবে আহরণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।
স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় পর্যাপ্তসংখ্যক বাংলা বইয়ের অভাব ছিল। বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করা এবং বিদেশি বই বাংলায় অনুবাদ করার জন্য বাংলা একাডেমিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু বাংলা একাডেমি সেই দায়িত্ব পালনে সফল হয়নি। আমরা যারা শিক্ষক-গবেষক, তারাও চাহিদা পূরণের মতো প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ রচনা করতে পারিনি। এমনকি স্বাধীনতা অর্জনের এতদিন পরও আমাদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাংলা বইয়ের অভাব দূর করা সম্ভব হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের বিদেশি ভাষায় লিখিত বই, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় লেখা বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ভাষাগত দুর্বলতার কারণে ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পক্ষেই তা সঠিকভাবে আত্মস্থ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জ্ঞানের প্রবাহ যেভাবে বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। কারণ জ্ঞানার্জনের জন্য বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। বই থেকেই জ্ঞানার্জনের নানা উপকরণ পাওয়া সম্ভব। ক্লাসরুমে শিক্ষকের দেওয়া বক্তব্য থেকেও জ্ঞানার্জন করা সম্ভব। তবে যে শিক্ষক ক্লাস নেবেন, তার প্রস্তুতির জন্য বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই জ্ঞানার্জনে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু আমাদের এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গুণমানসম্পন্ন বই পাওয়া যায় না।
আগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রন্থাগারে গিয়ে জ্ঞান আহরণের উদ্যোগ লক্ষ করা যেত। এখন এই প্রচেষ্টা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নোট মুখস্থ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এভাবে তো আর প্রকৃত জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয় না। যদি বই পড়ে বুুঝতে না পারে, তাহলে জ্ঞান আহরণ করবে কোত্থেকে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় দলীয়করণের কারণেও উচ্চশিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দলীয় বিবেচনায় তুলনামূলক কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষককে ভাইস চ্যান্সেলর বা এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নের চেয়ে সরকারের তোয়াজ করে পদ টিকিয়ে রাখার প্রবণতাই বেশি লক্ষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষক নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও দলীয় আনুগত্যের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে ভাইস চ্যান্সেলর বা এ জাতীয় পদে আসীন হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। আর একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম শিক্ষকতা করা। দেশে প্রচুরসংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের মতো উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। তারা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেন। এসব শিক্ষক নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাস না নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় দেন।
এর প্রেক্ষিতে আমি অনতিবিলম্বে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের প্রস্তাব করছি।
লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত
অনুলিখন : এম এ খালেক