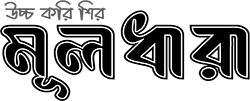জীবিকা অর্জনের জন্যে সম্ভাব্য পেশাগত কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ এক বিশেষায়িত শিক্ষাপদ্ধতিকে আমরা জানি কর্মমুখী শিক্ষা হিসেবে। এটা মূলত শ্রমবাজার, কর্মস্থল ও চাহিদা সামনে রেখে ঠিক করা হয়ে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রার ধরন ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পরিবর্তন এবং জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এর গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব ও চাহিদা দিন দিন বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে নিওলিবারেল, তথা নয়া উদারতাবাদের সম্প্রসারণ। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন পুরো বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। প্রয়োজনে মুহূর্তেই বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে থাকা কারো সঙ্গে অতি সহজে যোগাযোগ করা যায়। এর মাধ্যমে শুধু কুশল বিনিময় নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিক্ষাও প্রভাবিত হয়েছে বহুলাংশে। প্রভাব পড়েছে শ্রমবাজারের ওপরও।
মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাবকেও এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যেতে পারে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় পুরো বিশ্বের চাহিদা ও শ্রমবাজারে পার্থক্য থাকছে খুব সামান্য। তাই উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতেও কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব ও চাহিদা বাড়ছে ক্রমাগত। এদিকে বিশ্বের নানা দেশে জনশক্তি রপ্তানি করে বাংলাদেশ যে রেমিট্যান্স অর্জন করছে, সেখানেও এই শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার বিকল্প নেই। সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব শ্রমবাজারে নিজেদের অবস্থান অটুট রাখার পাশাপাশি আরো শক্তিশালী করার জন্যই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করা উচিত। বাংলাদেশের মতো রেমিট্যান্সনির্ভর দেশে জনশক্তিকে প্রকৃত কর্মক্ষম করার জন্য এবং বিদেশে অবস্থান টেকসই করার লক্ষ্যমাত্রায় কর্মমুখী শিক্ষা একান্ত জরুরি।

আমরা জানি, বর্তমান বিশ্বের শ্রমবাজারে সার্টিফিকেট তথা সনদের থেকে কর্মক্ষমতা তথা দক্ষতা বা স্কিলের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বহুজাতিক বৃহত্ কোম্পানি থেকে শুরু করে মধ্যম বা ছোটখাটো কোম্পানিগুলো তাদের কর্মীর বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতাকে গুরুত্ব দেয়। ইন্টারন্যাশনাল জায়ান্টরা কর্মীর দক্ষতাকে প্রতিনিয়ত মূ্ল্যায়ন করতে থাকে। কাজের বর্তমান ও অনাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মীর দক্ষতার ওপর নির্ভর করে তার টিকে থাকা।
একটা সময় যে-ই শ্রম নির্ধারণ করা হতো কর্মঘণ্টা হিসেবে, সম্প্রতি সেটাকে সক্ষমতার মানদণ্ডে যাচাই করার চেষ্টা চলছে। বর্তমানে অপেক্ষাকৃত স্কিলড কর্মী অনেক আনস্কিলড কর্মীর তুলনায় কম সময় কাজ করেও কয়েক গুণ বেশি বেতন পাচ্ছে। দক্ষ কর্মীর দক্ষতাকে আরো শানিত করার প্রয়োজনীয়তাকেও উসকে দিয়ে নির্দেশনা জারি করছে। আর এগুলোর চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে আমরা কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ার কথা হূদয়ঙ্গম করতে পারি। চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির মূল কারণটা কর্মীর দক্ষতা ও অদক্ষতার প্রশ্নে। আমরা শুরু থেকেই অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে কম আয় করি। তার বিপরীতে অন্য অনেক দেশ বহুগুনে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে অনেকটাই পাকাপোক্ত অবস্থানে চলে গেছে। শুধু টেকসই কর্মমুখী শিক্ষার কারণে ভারত, ভিয়েতনাম ও চীনের কর্মীরা উন্নত বিশ্বের বেশির ভাগ শ্রমবাজার নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছেন।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে বেকার রয়েছেন ২৫ লাখ ৯০ হাজার। ২০২৩ সাল শেষে এই সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৭০ হাজার, অর্থাত্ গত বছরের তুলনায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য একটি পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতি ১০০ জন স্নাতক ডিগ্রিধারীর মধ্যে ৪৭ জনই বেকার অর্থাত্ প্রতি দুজনে একজন। এর কারণগুলো জানলেও প্রতিকারের জন্য যথাযথ কোনো ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে পারিনি। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নোট বা গাইড-বইনির্ভর বা মুখস্থনির্ভর হয়ে আছে। পড়ছি আর শুধু মুখস্থ করে চলছি। না বুঝে পড়া আর শুধুই মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে নিজের চিন্তাশক্তি পুরোপুরি বিলীন করে ফেলছি। না কোনো দিকনির্দেশনা নিচ্ছি, না কোনো স্বপ্ন দেখছি। সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা, এমনকি স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিও লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি আর বিকশিত হওয়ার তেমন সুযোগ পাচ্ছে না।
বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া আমাদের জাতীয় দায়িত্বের প্রধানতম অংশ। সরকারিভাবে অব্যাহত প্রচেষ্টার পরও জনগোষ্ঠীর বৃহত্ একটি অংশকে এখনো মানসম্মত শিক্ষার আওতায় আনা যায়নি। এ অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক শিক্ষা, সেবামূলক এবং পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা প্রদান একান্ত জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে সামাজিক শিক্ষা এবং সামাজিক সেবার মান উন্নত করতে হবে।
প্রয়োজন আজ সমন্বিত ও আদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, যে ব্যবস্থায় থাকবে অগ্রাধিকার, পাবে যুগোপযোগী হাতে কলমে বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা। সনদধারী অথচ মূর্খতার যুগ থেকে পরিত্রাণ পেতে এর বাইরে তেমন আর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। তবে আশার কথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কিছু উদ্যোগ ইতিমধ্যে দেখা মিলছে, যাতে করে কিছুটা হলেও আশার আলোর সন্ধান পাওয়া যায়।
আমাদের দেশের অনেক কৃষিবিজ্ঞানী বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানাগারে প্রধান বিজ্ঞানী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কেউ কেউ চিকিত্সাবিজ্ঞানে উত্কর্ষ দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে অনেকে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও ভূতত্ত্বে স্ব স্ব দক্ষতা দেখিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। টেক জায়ান্ট গুগল থেকে শুরু করে আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে বাঙালিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। বাংলাদেশিদের অনেকে সরাসরি নাসায় গিয়েও যুক্ত হয়েছেন, বিষয়টি আমাদের কাছে অজানা নয়। যখন চারদিক থেকে হতাশার অন্ধকার গ্রাস করে, তখন বাংলাদেশি বিদগ্ধজনদের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলো একটু হলেও আমাদের শান্তিতে বাঁচার আশা জাগায়।
বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর বিরাট ভূমিকা রাখার কথা। তবে বর্তমানে তাদের বেশির ভাগের অবস্থা করুণ। ল্যাবরেটরি ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই এমনকি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণও নেই। রাজধানীর বাইরে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা চলছে নামসর্বস্ব অবস্থায়। এসব প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামের অবস্থাও প্রতিষ্ঠানের মতোই পশ্চাত্পদ। কিন্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নত করা গেলে তা কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে গুরুপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে আমরা বিদেশে যে জনশক্তি রপ্তানি করি, তারা নিজেরা যেমন উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাবে, তেমনি তাদের বাড়তি আয় প্রভাব রাখতে পারবে আমাদের রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে।
যুগের প্রয়োজনে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের কারিগরি শিক্ষায় ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবোটিকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, ইন্টারনেট অব থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন টেকনোলজির মতো আধুনিক বিষয়গুলো কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত নেই। এদিকে রোবোটিক্স মেইনটেন্যান্স, কন্ট্রোল সিস্টেম মেইনটেন্যান্স সাপোর্ট, ওয়েস্ট রি-সাইক্লিং, সোলার এনার্জি ও রিনিউয়্যাবল এনার্জির মতো বহু নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা অতি জরুরি। কর্মসংস্থানমুখী এসব বিষয় দ্রুত চালু করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।
চীন কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে খুবই তত্পর দেশগুলোর মধ্যে একটি। ২০০১ সালে চীনে ১৭ হাজার ৭৭০টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান ছিল; যাতে অধ্যয়নরত ছিলেন ১ কোটি ১৬ লাখ ৪২ হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী। তাদের কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ফলে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের পণ্য। অথচ বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার দুরবস্থাই আমাদের সম্মুখ এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বে লেদার, প্লাস্টিক, মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিকস, অটোমোবাইল, এয়ারলাইনস, নার্সিং ইত্যাদি খাতে চাহিদা থাকলেও পর্যাপ্ত আসনসংখ্যার অভাবে এসব খাতে কারিগরিভাবে দক্ষ পর্যাপ্ত মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে না। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বরং বাংলাদেশি অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ শ্রমিকই বিদেশে পাঠাতে বাধ্য হতে হয়। অথচ বিশ্ব শ্রমবাজারে অন্যান্য দেশ থেকে কিন্তু দক্ষ জনশক্তিই যাচ্ছে নিয়মিত। এই দক্ষ শ্রমবাজারটা ধরতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি।
বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু পাশ করা আর সনদ অর্জনেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না, বরং এটাকে করতে হবে কর্মমুখী। বিশেষত, বাংলাদেশের সেবা খাতের উন্নয়নে আগামী দিনের শিক্ষাকে খোলনলচে সংস্কার করতে হবে। খাতওয়ারি ধরে ধরে উপযোগিতাগুলো নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে নিয়ে তারপর সংস্কারে হাত দিতে হবে; অর্থাত্ কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা নিলে কর্মক্ষেত্রে কোন কোন ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা জরুরি। কৃষিশিক্ষা, প্যারামেডিক্যাল ও ভেটেরিনারি ট্রেনিং, নার্সিং ও ডেন্টাল ট্রেনিং, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির উন্নয়নে সবার আগে কাজ করতে হবে। এদিকে কোনো পেশাই যে ছোট নয়—সন্তানের এমন মানসিকতা তৈরিতে অভিভাবকদের নিবিড়ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, যাতে করে শিক্ষার্থীরা সনদনির্ভর প্রচলিত শিক্ষার তুলনায় কারিগরি ও জীবনমুখী শিক্ষাকে আরো গুরুত্ব দেয়।
লেখক : অধাপক, গবেষক এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার