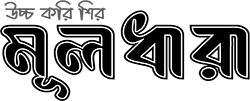সুশাসন, ন্যায়বিচার এবং উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে দক্ষ ও পেশাদার আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অপরিহার্য। তবে বর্তমান আমলাতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি, দক্ষতার অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার ঘাটতি বিদ্যমান। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আদর্শ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। তবে এর জন্য ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।
সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার আধুনিক সমাজে আমলাতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, একটি আদর্শ আমলাতন্ত্রের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি। তার মতে, আদর্শ আমলাতন্ত্রের ভিত্তি হলো আইনের শাসন এবং কর্তৃত্বের বৈধতা (Legal-Rational Authority)। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃত্বের এই বৈধতার ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান আমলাতন্ত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে অনেক সময় এই বৈধতা ব্যাহত হয়। ক্ষমতা প্রয়োগ এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি উপেক্ষা করা হয়। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রে ‘লিগ্যাল-রেশনাল অথরিটি’ প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে প্রশাসন পরিচালনার একটি কাঠামো তৈরি করতে হবে, যেখানে সব কর্মকাণ্ড আইনি কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হবে। পাশাপাশি, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং পদোন্নতি প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। আমলাতন্ত্রে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক সংযোগের চেয়ে দক্ষতা, মেধা এবং পেশাদারিত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক আনুগত্য বা ব্যক্তিগত সংযোগের প্রভাব লক্ষ করা যায়, যা আদর্শ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা। যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হলে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে কর্মকর্তাদের নির্বাচন করা প্রযোজন। যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগ এবং পদোন্নতি ব্যবস্থা আমলাতন্ত্রে পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশাসনের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।
আমলা নিয়োগের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করা—বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিসিএস পরীক্ষা কতটা বিজ্ঞানসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত তা প্রশ্নবিদ্ধ। এটি পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত নয়, বরং একটি ছদ্মবেশী বৈষম্যপূর্ণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত অনিয়ম। ২৬টি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাডারের জন্য যোগ্য প্রার্থী বাছাইকরণের এই অভিন্ন বিসিএস পরীক্ষার ধরন কতটা যথার্থ? ২৬টি ক্যাডারের জন্য যেসব ন্যূনতম অভিন্ন যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, সেসবই প্রিলিমিনারি টেস্টের মাধ্যমে যাচাই করা বিজ্ঞানসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত। চলমান প্রিলিমিনারি টেস্ট কি সেই অভিন্নযোগ্যতা ও দক্ষতা নিরূপণ করতে সমর্থ্য? উত্তর হলো, না! ২৬টি ক্যাডারের প্রত্যেকটিতে কি কাজ করতে হয়, তার জন্য কি দক্ষতার দরকার হয়, কোনো কোনো বিষয়ে অভিন্ন দক্ষতা থাকা উচিত সেটি নির্ণয়ের জন্য ঐ বিষয়ের মুখস্থবিদ্যাভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট হতে পারে না। এটি তাই প্রিলিমিনারি টেস্টের একটি বড় সংজ্ঞাগত দুর্বলতা।
বিশেষ ক্যাডারে কর্ম সম্পাদনের যে ধরনের দক্ষতা ও মানসিক সক্ষমতার দরকার হয় প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রশ্ন তা যাচাইয়ের জন্য কোনোভাবে যথার্থ নয়, বরং অপ্রাসঙ্গিক। সহজভাবে বললে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে ঐ নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতার প্রয়োজন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি প্রশ্ন হাস্যকরও বটে। একজন চিকিত্সকের বিসিএস ক্যাডারের জন্য সাহিত্যের প্রশ্ন কতখানি প্রাসঙ্গিক? এককথায় প্রিলিমিনারি টেস্ট দক্ষতানির্ভর নয়, বরং মুখস্থবিদ্যানির্ভর। ফলে দেখা যায়, ক্যাডাররা ‘Jack of all trades, master of none’।
সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে থাকেন বিসিএস ক্যাডার অফিসাররাই। ফলে সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশেই এই ক্যাডার অফিসারদের ওপরই নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের বিষয়টি মাথায় রেখেই সেকেলে পরীক্ষাপদ্ধতি থেকে বেরিয়ে পিএসসির উচিত বিসিএসের সিলেবাসের আধুনিকায়ন ও পরীক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার।
উন্নয়নকামী একটি রাষ্ট্রের সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে লোকপ্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল। চার্লস এ বিয়ার্ড সুশাসন ও উন্নয়নে লোকপ্রশাসনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, “The future of civilized government, and even I think, of civilization itself rests upon our ability to develop a science and philosophy and a practice of administration competent to discharge the function of civilization of civilized society.”
এজন্য লোকপ্রশাসন বিষয়কে বিসিএসের প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসে সম্পৃক্ত করতে হবে। লোকপ্রশাসন বিষয়ে বিশেষায়িত পরীক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে, এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে প্রশাসন ক্যাডারের জন্য একজন প্রার্থী অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
মনোবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে কোনো মানুষই মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। আপাতদৃষ্টিতে একজন মানুষকে মানসিকভাবে সুস্থ মনে হলেও অবচেতন মনে তিনি কোনো মেন্টাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হতে পারেন। চিন্তার (Content of Thought) এবং চিন্তার পদ্ধতি (Method of Thinking) এক কথা নয়। কথা বলতে গিয়ে আমরা চিন্তার বিষয় নিয়ে বাগিবতণ্ডায় আটকা পড়ে যাই, কিন্তু আমরা কেন বা কীভাবে এমন চিন্তাটি করলাম বা কোন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে চিন্তা করে এমন চিন্তার বিষয় উপনীত হলাম তা ভেবেও দেখি না। অনেক সময় আমরা যুক্তিহীনভাবে আমাদের নিজস্ব মানসিক ধারা বা সেট (Mind Set) অনুযায়ী সৃষ্ট প্রভাবে তৈরি হওয়া চিন্তার বিষয়-ভাবনা দ্বারা আবেগতাড়িত আচরণ, এমনকি ত্রুটিপূর্ণ আচরণও করে বসি। আর তাতেই ঘটে যায় নানা অঘটন। আমরা যা কিছু ভাবি না কেন তার নেপথ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক সত্তা। এজন্য বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে বিশেষ বোর্ড গঠন করে আনুষঙ্গিক সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব প্রার্থীকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করতে হবে তিনি সুনির্দিষ্ট ক্যাডারের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগী কি না।
প্রশাসন নিয়ে অনেকেরই আগ্রহ। বিশেষ করে বিসিএসে। এটাকে নানা কারণে মনে করা হয় ক্যাডার। এই ক্যাডার শব্দটির সঙ্গে নেগেটিভিটি থাকে। ক্যাডার শব্দটি বাদ দিয়ে যার যে সার্ভিস যেমন- সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সিভিল সার্ভিস হেলথ, সিভিল সার্ভিস অ্যাগ্রিকালচার এ রকম হোক। এটা আমাদের বড় সংস্কার।
জনপ্রশাসনে মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা/আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে, যাতে সহজেই সেটি পরিবর্তন করা না যায়। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়রেখা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। দ্বৈত পরীক্ষকের বিধান চালু করা দেরি হওয়ার একটি বড় কারণ, বিশেষ করে যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় দেওয়ার মতো পরীক্ষকের অভাব থাকে। এই নিয়ম ‘আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত’, কিন্তু মাত্র কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিসিএস উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট যোগ্য শিক্ষক রয়েছেন। পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য যে সময় লাগে সেটাও বেশ দীর্ঘ। বর্তমানে পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন করতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। এটা দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে করা যেতে পারে। আগে এমনই ছিল। যেটা দরকার তা হলো চাকরিপ্রার্থীরা ফৌজদারি মামলার আসামি কি না, সেটা যাচাই করা। বর্তমানে এই যাচাই প্রক্রিয়ায় চাকরিপ্রার্থীদের আত্মীয়দের ব্যাকগ্রাউন্ড ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয়, যা অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া, অনেক সুপারিশকৃত প্রার্থীও তাদের আত্মীয়স্বজন বা পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে বাদ পড়ে যান, যা কোনোক্রমেই কাম্য নয়।
দেশে এখন শিক্ষিতের হার বেড়েছে, শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, সে কারণে বিসিএসের আওতাও বাড়তে পারে। দেশের জনকল্যাণ চিন্তা থেকে বিসিএস পরীক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে—সে প্রত্যাশাই জনগণের। বিসিএস পরীক্ষা আজ এদেশে বিপদ এবং আপদ দুটোই। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো যেমন সুযোগ্য দিকনির্দেশনার অভাবে বিপদের মুখে পতিত হচ্ছে, তেমনি সে জায়গাগুলোতে অদক্ষ প্রার্থীর পদচারণা হেতু আপদেরও অন্ত নেই। দেশের জন্য এ পরিস্থিতি এক ভয়াবহ অস্তিত্বের সংকট, অনতিবিলম্বে তাই প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার। বিসিএস পরীক্ষার যথাযথ সংজ্ঞায়ন এবং এ প্রেক্ষিতে সময়োপযোগী বিষয়বস্তু ও মানবন্টন নির্ধারণ এখন অতীব জরুরি।
Common Sense বা কাণ্ডজ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার না করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে Psychometrics-এর জ্ঞানসম্পন্ন দেশ বা বিদেশের বিজ্ঞজনদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ঠিক করা উচিত, বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি কেমন হবে।
লেখক : ফিকামলি তত্ত্বের জনক শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক